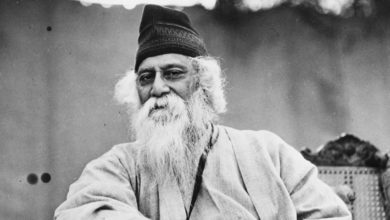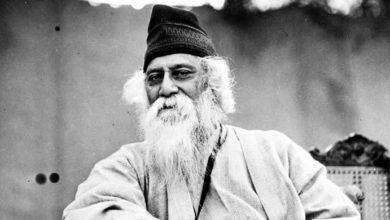ফিচার
রাসায়নিক যুদ্ধাস্ত্রের বিভীষিকা

১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট জাপানের হিরোসিমায় ফেলা পারমাণবিক বোমার নাম ‘লিটল বয়’ বা ছোট্ট বালক (বাচ্চা ছেলে) সন্দেহ নেই, নামটি খুবই কৌতুককর। কৌতুক তো বটেই, সভ্যতার ইতিহাসে মানবতার প্রতি এমন অমানবিক ঘটনা নজিরবিহীন।
বালকসুলভ বালখিল্যতা আর কাকে বলে! লিটল বয় বা বাচ্চা ছেলের মতোই দায়িত্বজ্ঞানহীন ছিল মানবতা আর সভ্যতার বিরুদ্ধের হত্যা ও ধ্বংস। এখন সেই পারমাণবিক ‘লিটল বয়’ সাবালকত্ব পেয়ে আরো ভয়ঙ্কর ‘রাসায়নিক যুদ্ধাস্ত্রের বিভীষিকায়’ মানুষ ও মানবতাকে নিত্য তাড়া করে ফিরছে।
এ কথা সবাই স্বীকার করছেন যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন যুদ্ধবাজদের কাণ্ডজ্ঞানহীন ঘটনার পরিসমাপ্তি সেখানেই ঘটেনি; আরও সামনে এগিয়েছে। সেদিনের সেই লিটল বয় আজ আর নেই বটে, বরং সে এখন পূর্ণ সাবালক হয়ে গিয়েছে। সাবালকত্ব এতটাই অক্টোপাসরূপী বিভীষিকার চেহারা ধারন করেছে যে, এই সাবালকের হাতে এখন কতগুলো পারমাণবিক বোমা রয়েছে সে হিসাব রাখাটাও কষ্টকর। হিরোসিমার ‘লিটল বয়’ আর নাগাসাকির ‘ফ্যাটম্যান’ নামের পামাণবিক বোমা বিস্ফোরণের পর যদিও দীর্ঘদিন অতিক্রান্ত, তথাপি মানব সভ্যতার আকাশে আশঙ্কার কালো মেঘের বিস্তার বন্ধ হয়নি; বেড়েই চলেছে।
হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ মানব ইতিহাসের এক কলঙ্কতম অধ্যায়; ন্যক্কারজনক ঘটনা। এহেন জঘন্য অপরাধের নিন্দার ভাষাও মানবতার অজানা। প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে সেই ভয়ঙ্কর ঘটনার বিবরণ যখন জানা যায়, তখন খোদ মানবজন্মই নিজের প্রতি ঘৃণা ও লজ্জায় কুঁকড়ে যায়।
একবার ইউনেস্কো এবং জাপানের কয়েকটি সংস্থার যৌথ উদ্যোগে হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে আন্তর্জাতিক সন্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শহর দুটিতে পারমাণবিক বিস্ফোরণের পর দীর্ঘবছর ধরে উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটেছে, সেটা পর্যালোচনা করাই ছিল সন্মেলনের মূল উদ্দেশ্য।
যা জানা গেল, তা হল, পারমাণবিক বিস্ফোরণ ও রাসায়নিক যুদ্ধাস্ত্রের কুফল-তালিকা সম্পর্কে অনেক তথ্যই এখনও মানব জাতির, এমন কি, বিজ্ঞানিদের পর্যন্ত অজানা। সবটুকু জানা গেলে তবেই বোঝা যাবে, পারমাণবিক ও রাসায়নিক অস্ত্র ও যুদ্ধের পরিণতি মানব সভ্যতার জন্য কতটুকু ক্ষতিকর ও সুদূরপ্রসারী। তবে এই কথা অস্বীকার করার জো নেই যে, পারমাণবিক বিস্ফোরণের কুফল সম্পর্কে এখন পর্যন্ত যতটুকু আলাপ-আলোচনা হয়েছে, তাতে কিছু হলেও তথ্য-উপাত্ত জানা গেছে। কিন্তু রাসায়নিক যুদ্ধাস্ত্রের ভয়াবহ ও মর্মন্তুদ পরিণতির ব্যাপারে বলতে গেলে কিছুই জানা সম্ভব হয়নি।
ভয়াবহতার কারণেই সবাই মিলে ‘নন-প্রলিফারেশন অব নিউক্লিয়ার ওয়েপেন্স’ বা ‘পারমাণবিক অস্ত্রের নিষিদ্ধকরণ’ প্রস্তাবটি জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত হয়েছে অনেক আগেই। কিন্তু এই কাগুজে প্রস্তাবের ফলে কাজের কাজ কতটুকু হয়েছে, সেটাই এক বিরাট বড় প্রশ্ন ও বির্তকের বিষয়।
কারণ, একই সঙ্গে ‘নন-প্রলিফারেশন অব কেমিক্যাল ওয়েপেন্স’ বা রাসায়নিক অস্ত্রের নিষিদ্ধকরণের বিষয়টিও অনেক বেশি জরুরি। মনে রাখতে হবে যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রায় এক লক্ষ টনের উপর বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয়েছিল। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল দশ লক্ষেরও বেশি মানুষ। এখনও বিশ্বের বৃহৎ শক্তি গোষ্ঠী লক্ষ লক্ষ টন ঠঢ, ইপ্রাইড, ডি-এম, সারি, সোমান ইত্যাদি মারাত্মক রাসায়নিক অস্ত্র তৈরি করছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এহেন উন্মাদনা মাতালের মতো বেড়ে চলেছে। ভিয়েতনাম, পারস্য উপসাগরীয় যুদ্ধ, ইরাক, সিরিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, আফগানিস্তানের সংঘর্ষে সেসবের প্রমাণ পাওয়া গেছে।
রাসায়নিক যুদ্ধাস্ত্র সম্পর্কে কিছুদিন আগেও সাধারণত এই ধারণা প্রচলিত ছিল যে, এই অস্ত্র শুধু মানুষের বিরুদ্ধেই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। যেখানেই রাসায়নিক অস্ত্র প্রয়োগ করা হয়েছে, সেখানকার জৈবিক পরিবেশ তো ধ্বংস হয়েছেই, এমন কি সেখানকার সমস্ত প্রাণী, উদ্ভিদ এবং সজীব বস্তুর জীবনই বিপন্ন হয়েছে। যেভাবে বৃহৎ রাষ্ট্রশক্তিসমূহ তাদের রাসায়নিক অস্ত্রের সম্পদ ভাণ্ডার বাড়িয়ে চলেছে, তাতে মুক্ত ও নির্মল পরিবেশে ফিরে আসার পথটি ক্রমে ক্রমে খুবই দুর্গম হয়ে উঠছে।
যুদ্ধাস্ত্র হিসাবে রাসায়নিক সামগ্রীর প্রথম ব্যবহার হয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধে। ১৯১৫ সালে জার্মানরা পোলান্ড ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্রথমবারের মতো ক্লোরিন গ্যাস ছোঁড়ে, যদিও তাঁতে বিশেষ সুবিধা হয়নি। ঐ বছরের এপ্রিল মাসে জার্মানরা বেলজিয়ামের ইপ্রেস নামে এক জায়গায় যে বিষাক্ত রাসায়নিক গ্যাস ব্যবহার করেছিল, তার রংটা ছিল ফিকে লাল এবং দ্রব্যটা অনেকেরই কাছে অপরিচিত ছিল।
ধারণা করা হয়, খুব সম্ভবত এই গ্যাস ক্লোরিন ও ব্রোমিন গ্যাসের সংমিশ্রণে প্রস্তুত করা হয়েছিল। এই জার্মানরাই একই বছর, অর্থাৎ ১৯১৫ সালের ২২ এপ্রিল ফরাসি ও ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীকে রাসায়নিক অস্ত্রের সাহায্যে একেবারে কাহিল বানিয়ে প্রায় জয়লাভই করে ফেলেছিল। এক সময় সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাস ও আর্সেনিক ক্লোরাইড গ্যাসের বিষবাষ্প জার্মানরা তৈরি করে শত্রু সৈন্যের দিকে হেনেছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের সৈন্যরা পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লে এই মারাত্মক রাসায়নিক বিষবাষ্প ছড়িয়ে দেওয়া হত। বিষবাষ্প ছড়ানোর সময় লক্ষ্য রাখা হত যেন ওটা বাতাসের চেয়ে বেশি ভারী হয়। না হলে তা হাল্কা হয়ে উপরে উঠে গেলে আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে।
একবার বিষবাষ্প ছোঁড়ার সময় ভারি মজার ব্যাপার ঘটেছিল। শত্রুপক্ষের দিকে জার্মানরা যখন মহানন্দে বিষাক্ত গ্যাস ছড়াচ্ছিল তখন হঠাৎ বাতাসের গতি উল্টে যায়। বিষবাষ্প এসে জার্মান সৈন্যদের তখন একেবারে নাজেহাল করে দিয়েছিল।
বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, বিষবাষ্পের মধ্যে ফসজিন বা কার্বনিল ক্লোরাইড অত্যন্ত বিষাক্ত গ্যাস। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অভিজ্ঞতায় আরো মারাত্মক কিছু করার অভিলাষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এই গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছিল। ক্লোরো-পিকরিন ও সায়ানোজেন গ্যাসও খুব মারাত্মক। সায়ানোজেন গ্যাস চোখে ঢুকলে সঙ্গে সঙ্গে চোখ অন্ধ হয়ে যায়। এরপর ব্রোমিন বাষ্প, কার্বন-ডাই-সালফাইড, অ্যান্টিমনি ক্লোরাইড, টিন ক্লোরাইড, সালফুরেটেড হাইড্রোজেন, ব্রোমো অ্যাসেটিক ইস্টার, ডাই ফিনাইল ক্লোরো আরসাইন (ডি-এম), ক্লোরো অ্যাসিটোফিনোন (সি-এন), ক্লোরোসালফোনিক অ্যাসিডের বিষাক্ত বাষ্প যুদ্ধক্ষেত্রে বহু সৈন্যের জীবন হানি ঘটিয়েছে। চিন-জাপানের যুদ্ধের সময়ও জাপানিরা চিনা সৈন্যদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের বিষাক্ত রাসায়নিক গ্যাস ব্যবহার করেছে। জার্মানরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মাস্টার্ড গ্যাস যথেচ্ছ ব্যবহার করেছে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, নার্ভ গ্যাস, যদিও এটা জার্মানরাই তৈরি করেছিল, তবু এই মারাত্মক গ্যাস কখনওই যুদ্ধক্ষেত্রে তারা প্রয়োগ করেনি।
বিষাক্ত রাসায়নিক বস্তুগুলোর বাষ্প শুধু যে কেবল শত্রু নিধনের জন্য ব্যবহার করা হয়, তা কিন্তু নয়। কৌশল হিসাবেও এর প্রয়োগ (অপপ্রয়োগ শব্দটিই হওয়া উচিত) লক্ষ্যণীয়। পরিষ্কার মেঘমুক্ত আকাশে উড়োজাহাজ উড়লেই শত্রুসেনারা টের পায়। অতএব, আর্সেনিক ক্লোরাইড, ক্লোরোসালফোনিক অ্যাসিড দিয়ে কৃত্রিম ধোঁয়া সৃষ্টির পরিকল্পনা করা হলো, যাতে সহজেই প্রতিপক্ষের চোখে ধুলা দেওয়া যায়।
এই গ্যাস জলীয় বাষ্পের সংস্পর্শে এলে ধোঁয়ার মেঘের সৃষ্টি করে। বিষবাষ্পের এই ভয়াবহ অস্ত্র সাধারণত দেহের যে কোনও অংশে আক্রমণ করতে পারে। যেখানেই এই গ্যাস স্পর্শ করবে সেখানেই একটা প্রদাহের সৃষ্টি হবে। ক্রমশ সেটা মারাত্মক আকার ধারণ করে সমস্ত দেহে ভীষণ বিপর্যয় ঘটাবে। মুখোস পরেও রাসায়নিক বিষবাষ্পের কবল থেকে রক্ষা পাওয়া শক্ত। এই রাসায়নিক গ্যাস শুধু যে নির্দিষ্ট যুদ্ধক্ষেত্র এবং সীমিত শত্রু সৈন্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তা নয়, বরং আশেপাশের বিস্তীর্ণ এলাকা ও জনবসতির মধ্যে দুষণ ছড়িয়ে সুদূরপ্রসারী কুপ্রভাব বিস্তার করে।
পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, রাসায়নিক যুদ্ধাস্ত্র শত্রু সৈন্যদের দেহের উপর অকল্পনীয় বিরূপ-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। পরবর্তী ধাপে ধীরে ধীরে স্নায়ুব্যবস্থা অবশ করে দেয়। দেহ ও মনে এর মারাত্মক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিবরণে শিউরে উঠতে হয়। শরীরের চামড়া, চোখ, কান, নাক, মুখ, ফুসফুস ইত্যাদি কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোনওটিও রেহাই পায় না। কখনও এমনও হয়েছে, আক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যু হয়নি বটে, কিন্তু চিরতরে বধির, অন্ধ অথবা একেবারে পঙ্গু হয়ে গেল।
ভিয়েতনামের যুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাসায়নিক যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহার করেছিল এবং এতো কিছুর পরেও চরমভাবে পরাজিত হয়েছিল। হাইড্রোজেন সায়ানাইডকে (এ-সি) বলা হয় ব্লাড গ্যাস। কেননা এটা রক্ত চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে থাকে এবং দেহের টিস্যুতে অক্সিজেন যোগান দিতেও প্রতিরোধ ঘটায়। ফসজিনকে এমন মারাত্মকরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে, কারণ, এটি স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসে দারুণ বিঘ্ন ঘটায়। মাস্টার্ড গ্যাস, এবং লিউসাইট (বিপজ্জনক আর্সেনিক যৌগ) হলো এমনই রাসায়নিক প্রক্রিয়া-প্রবন দ্রব্য, যা প্রাণীর (মানুষ ও পশু) সারা দেহে আরোগ্যহীন ফোস্কা এবং ক্ষেত্র বিশেষে বিষাক্ত ক্ষতেরও সৃষ্টি করে। সারি, সোমান এবং ভিএক্স-এই রাসায়নিক যুদ্ধাস্ত্রগুলো হচ্ছে নার্ভ রিয়েজেন্ট। এদের কাজ হলো দেহের স্নায়ুকে চিরদিনের জন্য অবশ করে দেওয়া। এছাড়াও যেসব মারাত্মক রাসায়নিক যুদ্ধাস্ত্রের খোঁজ জানা গেছে, তার মধ্যে কয়েকটি হলো-মিথাইল ফ্লুরো অ্যাসিটেট, প্যারাথিয়ন, ক্যাডমিয়াম অক্সাইড, সায়ানোজেন ক্লোরাইড, ফসফোলিন, ডাইঅক্সিন ইত্যাদি।
রাসায়নিক যুদ্ধাস্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ হিসাবে আবির্ভাব ঘটে গ্যাস মাস্কের। গ্যাস মাস্কে প্রধানত থাকে চারকোল এবং সোডালাইম। চারকোল অনেকখানি গ্যাস শুষে নিতে পরে আর সোডালাইম বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিষাক্ত গ্যাসকে প্রশমিত করে। গ্যাস মাস্কে অনেক সময় আবার যান্ত্রিক উপায়ে পরিস্রবণের ব্যবস্থা রাখা হয়, যাতে কঠিন কণার কোনও সূক্ষ্ম অংশ দেহে প্রবেশ করতে না পারে।
রাসায়নিক যুদ্ধাস্ত্রের কার্যকরী ব্যবহার নিয়ে যুদ্ধরত পক্ষসমূহ বুদ্ধি আর কৌশলের নানা খেলায় মেতে ওঠে। শত্রুপক্ষ অনেক সময় চালাকি করে রাসায়নিক ধোঁয়ার মেঘ সৃষ্টি করে নিজেদেরকে ঐ মেঘের আড়ালে লুকিয়ে রাখতে চায়। কিন্তু প্রতিপক্ষও দারুণ সেয়ানা-তাদেরও রয়েছে আনকোরা নতুন থার্মাল ইমেজার্স (টিআই), যার ভেতরকার সেনসিটিভ টেলিস্কোপের সাহায্যে ধোঁয়ার মেঘের পুরো আস্তরণের মধ্য দিয়েও প্রতিপক্ষকে সনাক্ত করতে অসুবিধা হয় না। উভয় পক্ষের বিচিত্র-সব রাসায়নিক দ্রব্যাদির বহুবিধ প্রয়োগের ফলে মূল অসুবিধাটুকু হয় মানুষ আর প্রকৃতির। ভুগতে হয় মানুষজন আর প্রকৃতি ও পরিবেশের নিরিহ সদস্যদেরকেই।
কথা এখানেই শেষ নয়। থার্মাল ইমেজার্স কায়দাকে কোণঠাসা করে দিয়ে আবার নতুন যে আবিষ্কার সম্পন্ন হয়ে গেছে, তার নাম ভিস্যুয়াল অ্যান্ড ইনফ্রারেড স্কিনিং স্মোক বা সংক্ষেপে ভিআইআরএসএস। এই যন্ত্রের সাহায্যে মাত্র দুই সেকেন্ডের মধ্যে বাতাসে ইনফ্রারেড আলোক শক্তি দিয়ে ঘন ধোঁয়ার আবরণ সৃষ্টি করা হয়। তখন থার্মাল ইমেজার্স দিয়ে হাজার তাকালেও শত্রু সেনাদের দেখতে পাওয়া যাবে না। একবিংশ শতাব্দীর সঙ্কটময়-সঙ্কুল পরিস্থিতিতেও বহু উন্নত (!) দেশের নামকরা (!!) বিজ্ঞানীরা মারাত্মক ধরনের রাসায়নিক যুদ্ধাস্ত্র আর বিষবাষ্প তৈরির আদিম উল্লাসে মেতে রয়েছেন!
রাসায়নিক যুদ্ধাস্ত্র (অপ) প্রয়োগের ক্ষেত্রে নীতি-নৈতিকতার বাছ-বিচার করার কথা কেউ ভাবছেই না। আরও আশঙ্কার সুযোগ রয়েছে মানব জাতির সামনে। যদি কখনও কোনও যুদ্ধোন্মাদ দেশ শত্রু নিধনের নামে টাইফয়েড, কলেরা, নিউমোনিয়া অথবা আমাশয়ের বিষাক্ত রোগজীবাণু শত্রুপক্ষের পানিতে বা বাতাসে ছড়িয়ে দেয় তখন পরিস্থিতি কত ভয়াবহ হবে? নানা ধরনের বিষাক্ত ভাইরাস ছড়িয়ে শত্রুপক্ষকে পঙ্গু ও বিপর্যস্ত করে দেওয়ার পৈশাচিক উল্লাসের বলি হতে হবে বহু সাধারণ মানুষ, প্রাণী ও উদ্ভিদ প্রজাতিকেও। কারণ রোগের ভাইরাস ইউনিফর্ম দেখে শুধু সৈন্যদেরকেই আক্রমণ করবে না।
বিষাক্ত রাসায়নিক গ্যাস, নিউক্লিয়ার অস্ত্র বা পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ সম্বন্ধে অল্পবিস্তর জানার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু গোপনে জীবাণু হামলা পরিচালনা করা হলে, সে খবর পাওয়া যাবে কিভাবে? জীবাণু লেলিয়ে দেওয়ার এই সর্বাধুনিক যুদ্ধকৌশল শুধু শত্রু সৈন্যদের দুর্বল, পঙ্গু ও পরাজিত করবে না-বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জীবনকেও ছিনিয়ে নেবে অতি সন্তর্পনে, ধীরে ধীরে। এটা অবধারিত যে, দেহের মধ্যে একবার জেনেটিক পরিবর্তন ঘটলে তার মারাত্মক বিষময় ফল বংশধারাতেও বর্তাবে। সমগ্র মানব সমাজের প্রাণ প্রবাহের অস্তিত্বের সঙ্কট সম্ভবত সবচেয়ে মারাত্মক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হবে।
কোনও কোনও গবেষক বলছেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রাসায়নিক বিষবাষ্প ছাড়াও দুরারোগ্য অ্যানথ্রাক্স রোগের জীবাণু শত্রু সৈন্যদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছে। এই জীবাণু অস্ত্রের কোড নাম দেওয়া হয়েছিল ‘এন’। এহেন কুবুদ্ধি কোনও নেতা বা দেশের মাথায় এখনও যে রয়ে যায় নি, সে কথা নিশ্চিন্তভাবে বলা সম্ভব নয়।
এমন সন্দেহরও কারণ রয়েছে। কিছুদিন আগে, স্কটল্যান্ডের এক দ্বীপে অ্যানথ্রাক্স রোগের জীবাণু ধ্বংস করার জন্য ফরমালডিহাইড ও সমুদ্রের নোনা জল সেখানকার মাটিতে ছিটিয়ে অ্যানথ্রাক্স নির্মূল অভিযান চালানো হয়েছিল। ১৯৪০ সালে যুদ্ধের মহড়ার সময় নাকি জীবাণুটির ব্যবহার হয়েছিল, যা অর্ধশতবর্ষ বাদে জেগে ওঠে। বারোজন বিশেষজ্ঞের একটি অ্যানথ্রাক্সবিরোধী টিম উপযুক্ত পোশাক ও প্রতিষেধক নিয়ে তবেই কাজে নামে।
ভিয়েতনামের যুদ্ধেও এই জেনেটিক অস্ত্র গোপনে ও সীমিত আকারে কাজে লাগানো হয়েছিল। কারণ, দেশটির বহু শিশু, নারী ও পুরুষ চিরকালের জন্য পঙ্গু ও অসুস্থ হয়ে গেছে এবং তাদের মাধ্যমে বিকলাঙ্গ প্রজন্মের প্রজনন হচ্ছে। সুদূরপ্রসারী সেসব প্রতিক্রিয়ার পুরো চেহারাটার বীভৎস রূপটি হয়তো এখনই সম্পূর্নভাবে স্পষ্ট হয়নি; যখন হবে, তখন মানবতার মধ্যে তীব্র হাহাকারের বিলাপ শুরু হয়ে যাবে, এ কথা নির্দ্বিধায় বলা চলে।
জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর কৌশল অবলম্বন করে বর্তমানে যেমন মানুষের কল্যণের জন্য ইন্টারফেন, ইনসুলিন, সোমাটসটাটিন, এইচ-জি-এইচ ইত্যাদি মূল্যবান ও জীবনমুখী ঔষধ তৈরি করা যায়, ঠিক তেমনি অনেক ‘বীভৎস-প্রাণঘাতী ভাইরাস’ তৈরি করাও সম্ভব।
বিজ্ঞান এতোটাই এগিয়েছে যে, আজকাল বিজ্ঞানীরা সহজেই কোনও ভাইরাসের নির্বাচিত অংশ কাঁচি দিয়ে কেটে নিয়ে তার সঙ্গে খুশিমতো অন্য কোনও জীন আঠার মতো জুড়ে দিতে পারেন। এর ফলেই তৈরি হয় ‘বীভৎস’ ভাইরাস। আসলে আক্ষরিক অর্থে কাঁচি দিয়ে তো আর ভাইরাস বা অন্য কোনও জীনের অংশ কাটা যায় না। এর জন্য চাই এক বিশেষ ধরনের এনজাইম। যে এনজাইম এই বিশেষ ধরনের সংযোজনের কাজটি সারতে পারে, তার নাম-রেসট্রিকসন এনজাইম। আর আঠা দিয়ে জীন যুক্ত করবার জন্য যে এনজাইমের প্রয়োজন, তার নাম-লাইগেজ। জেনেটিক অস্ত্রের আঘাত দেহে ঘটবে অতি নীরবে, অতি নিঃশব্দে-চট করে সেটা বুঝবার উপায়ও নেই। তাই জেনেটিক অস্ত্রের কথা স্মরণ রেখে আরেক দল বিজ্ঞানী তার থেকে আত্মরক্ষার জন্য নানা ধরনের পোশাক, যেমন প্রোটেকটিভ স্যুট, ইকুইপমেন্ট, ডি-কনটামিনেশন কিট, ক্যাসুয়ালিটি ব্যাগ-এই রকমের আরও কত কি উদ্ভাবন করতে লেগেছেন। কিন্তু বিপদের ভয়াবহতা ও গভীরতার কাছে এসব প্রতিষেধী উদ্যোগ নস্যি মাত্র।
মলিক্যুলার বায়োলজি, রিকমবিন্যান্ট ডিএনএ টেকনোলজি এবং জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর অতি সূক্ষ্ম কেরামতি একদিকে যেমন ‘বীভৎস ভাইরাস’ তৈরি করছে, অন্য দিকে এই জীন-প্রযুক্তি কৌশলের চালাকি খাটিয়ে মারাত্মক রাসায়নিক যুদ্ধাস্ত্রের প্রতিষেধকও তৈরি করা অসম্ভব নয়। বিজ্ঞানের এই সাধারণ সূত্র সকলেই জানেন যে, বিষাক্ত রাসায়নি বস্তু এবং দেহের প্রোটিনবাহী অণুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র ঘটার ফলে অক্সিজেন সরবরাহ বিঘ্নিত হয়। প্রায় সব বিষাক্ত বস্তুই দেহের নির্দিষ্ট সেলুলার রিসেপ্টরের (সিআর) সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। কিন্তু যেহেতু দেহের সিআর-এর সংখ্যা সীমিত, কাজেই আত্মরক্ষার সমস্যার ব্যাপারটিও সীমিত গণ্ডির মধ্যেই আবর্তিত।
পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন যে, প্রায় একশ’ নার্ভ গ্যাস থাকলেও তারা সকলেই একই সিআর-এর সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করে। যদি কোনও উপায়ে এই যোগসূত্র স্থাপনের কাজে বাধা দেওয়া যায়, তাহলেই মানব বংশ নার্ভ গ্যাসের বিভীষিকার কবল থেকে মুক্তি পাবে। এই মানব-মুক্তির মন্ত্রটিও কিন্তু জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর আওতার মধ্যে। বিষাক্ত রাসায়নিক বস্তুর সঙ্গে সংযুক্ত হয় যে সিআর প্রোটিন, তার জীনকে আলাদা করে তার ডিএনএ ব্লু-প্রিন্ট জেনে নেওয়া হয়।
এর পরের কাজ সহজ। এবার জীন-প্রযুক্তি কৌশল (রিকমবিন্যান্ট ডিএনএ টেকনোলজি) খাটিয়ে এমন একটা মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি তৈরি করা হয়, যেটা নাকি বিষাক্ত রাসায়নিক বস্তু বা টক্সিনের সঙ্গেও অনায়াসে জুড়ে যেতে পারে। ঠিক এই রকম পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞানীরা নার্ভ গ্যাসের প্রতিষেধকও আবিষ্কার করে ফেলেছেন। অন্য রাসায়নিক বস্তুর প্রতিষেধকও হয়ত ভবিষ্যতে আবিষ্কৃত হবে। সে চেষ্টাও করছেন মানব-কল্যাণকামী বিজ্ঞানীরা।
রাসায়নিক যুদ্ধাস্ত্র একেবারেই নিষিদ্ধ করা হোক-পৃথিবীর মানুষ এমন দাবি জানাচ্ছে বহুদিন ধরেই। এ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক, আলাপ-আলোচনাও কম হয় নি। প্রায়-প্রায়শই নিরস্ত্রীকরণ সন্মেলন হচ্ছে পরাশক্তিগুলোর মধ্যে। জাতিসংঘের তরফে প্রতিনিয়ত নিস্ফল আবেদন-নিবেদনও করা হচ্ছে যুদ্ধরতদের কাছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। আক্রমণকারী এবং আক্রান্ত-উভয়েই পরিপূর্ণভাবে অবগত রয়েছে যে, কোনও প্রকারের যুদ্ধই মানুষ-সমাজ-সভ্যতা-প্রকৃতিকে সমূহ ধ্বংসের পথে ঠেলে দেয়। যুদ্ধে রাসায়নিক যুদ্ধাস্ত্রের ব্যবহার সে ক্ষেত্রে আরও অধিক ক্ষতি ও ভয়াবহতা ঢেকে আনে। বিশেষ করে রাসায়নিক যুদ্ধাস্ত্রের কারণে তাবৎ বিশ্ব যে এক বিরাট পরিবেশ ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের অতল অন্ধকার গহ্বরের দিকে ছুটে চলেছে, সেটাও কারোই অজানা নয়।
রাজনীতির আপাত সাধুতার তলে শক্তির মদমত্ত লড়াই ক্রমেই পৃথিবীকে বসবাসের অনুপযোগী করে তুলছে। বিজ্ঞানের সামনেও এসে হাজির হয়েছে এক মহা চ্যালেঞ্জ-বিজ্ঞান মানুষের জন্য আর্শীবাদ না অভিশাপ-এই অমীমাংসিত তর্কের আশু সমাধানের জ্বলন্ত চ্যালেঞ্জ।
ড. মাহফুজ পারভেজ: কবি ও লেখক। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগে অধ্যাপনারত, mahfuzparvez@gmail.com